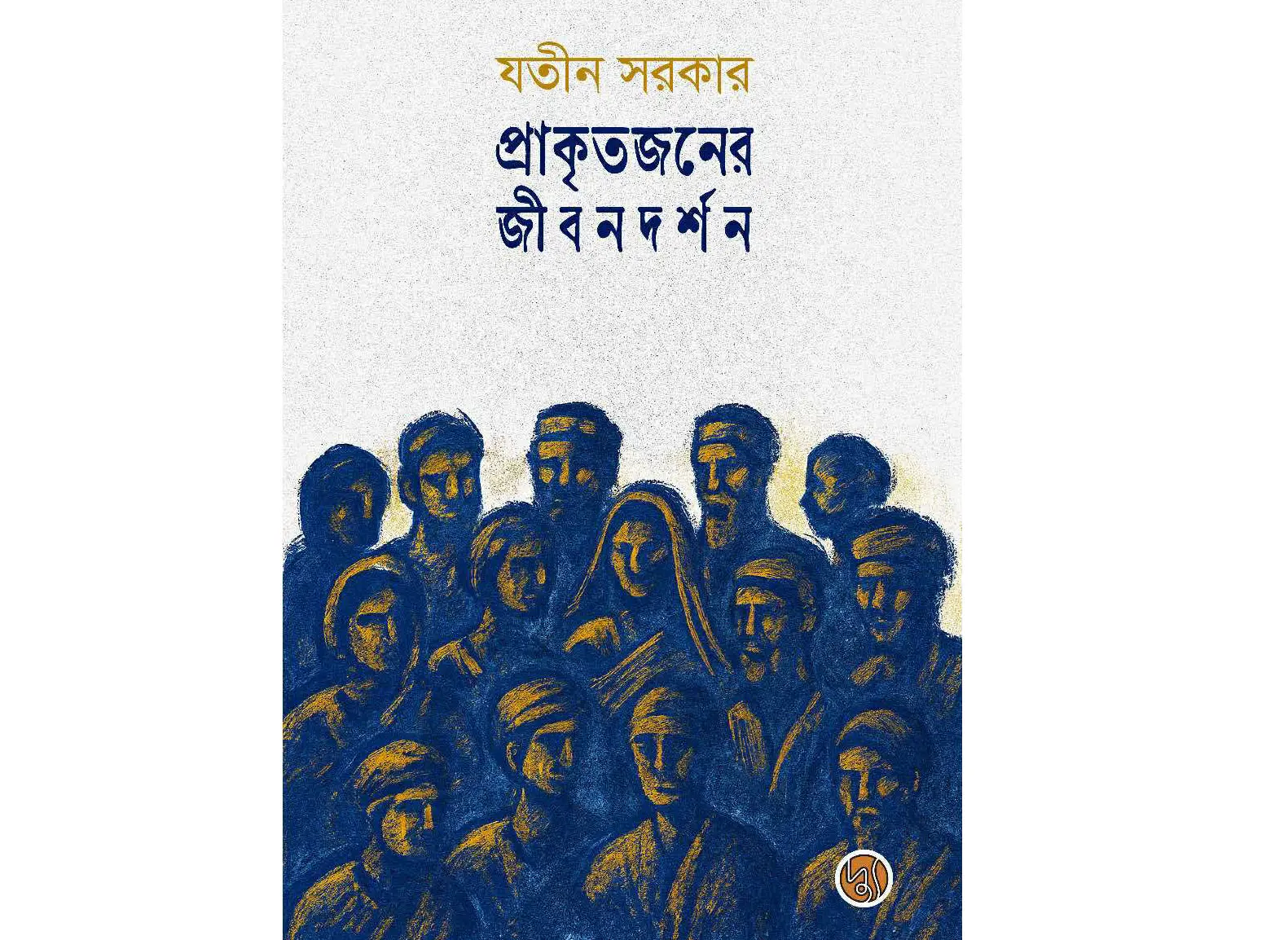প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন
লেখক: যতীন সরকার
প্রথম প্রকাশ: শোভা প্রকাশ, ঢাকা । ২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ: দ্যু প্রকাশন, ঢাকা।২০২৫
বাংলার সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী শ্রেণি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনবোধ, দর্শন এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের যে বিশ্লেষণমূলক ও জীবন্ত রূপ যতীন সরকারের লেখায় পাওয়া যায়—প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন সেই ধারারই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বই বা গবেষণা।
‘প্রাকৃতজন’ শব্দটি মূলত সাধারণ মানুষ—যারা সমাজের বৃহৎ সংখ্যক অংশ এবং বাস্তব জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করেন—তাদের নির্দেশ করে। বাংলা একাডেমির অভিধান অনুযায়ী এটি সাধারণ বা নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে নির্দেশ করে। সাবঅলটার্ন তত্ত্বের আলোকে এই ধারণাটি আরও ব্যপক হয়ে যায়—যেখানে ক্ষমতার মূল ধারার বাইরে থাকা, প্রতিনিধিত্বহীন, নিপীড়িত ও বাদ পড়া মানুষের অবস্থান, অভিজ্ঞতা এবং সংগ্রাম সামনে আসে।
আন্তোনিও গ্রামসি এবং গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মতো চিন্তাবিদদের আলোচনার ধারায়—এই শব্দটি ক্ষমতার কাঠামো থেকে বাদ পড়া মানুষের রাজনৈতিক-সামাজিক অস্তিত্বকে ইতিহাসে দৃশ্যমান করে তোলে। এই বই পড়ার আগে এই ধারণাগুলির সাথে পরিচয় থাকলে ‘প্রাকৃতজন’ অর্থটি বোঝা এবং তাদের দর্শনের ব্যাখ্যা পাঠে আরও স্পষ্টতা তৈরি হয়।
প্রাকৃতজনের জীবন কেবল দারিদ্র্য, বাঁচার সংগ্রাম বা পেশাভিত্তিক শ্রম নয়; বরং তাদের জীবনেই নিহিত এক বাস্তববাদী, মানবিক এবং যুক্তিনির্ভর দর্শন। জীবনের অর্থ, সমাজ-সংগঠন, পারস্পরিক সহমর্মিতা, শ্রমে সৃজনের আনন্দ—এসবই প্রাকৃতজনের দর্শনের ভিন্ন রূপ। তারা অবাস্তব ধর্মীয় চমৎকারবাদ বা বিমূর্ত তত্ত্বের পেছনে নয়—বরং বাস্তব জীবন, প্রকৃতি, সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতার মধ্যেই অর্থ খুঁজে নেয়। অন্যদিকে দর্শনের ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দর্শন মূলত অস্তিত্ব, যুক্তি, জ্ঞান, মূল্যবোধ এবং ভাষা সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্নগুলোর পদ্ধতিগত অধ্যয়ন। এটি কোনো বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ বোঝার জন্য যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া। দর্শনের আক্ষরিক অর্থ ‘দেখা’ বা ‘পর্যবেক্ষণ’ হলেও, এর প্রকৃত অর্থ কেবল দেখা নয়; বরং যা দেখা যায় তার গভীরে প্রবেশ করে তার মূল সত্য ও জ্ঞান অন্বেষণ করা। মহামতি কার্ল মার্কস মানব ইতিহাসকে এমন এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে মানুষ ধীরে ধীরে আত্ম-অনুধাবন, বিকাশ এবং স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যায়—আর এই পথ চলায় বিভিন্ন মানসিক, বস্তুগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধা অতিক্রম করে। তাঁর মতে দর্শন কেবল বিশ্বের ব্যাখ্যা নয়, বরং বিশ্বকে পরিবর্তনের হাতিয়ার। লেখক অবিরতভাবে নিমগ্ন থেকেছেন সেই চেষ্ঠায় এই বইটিতে।
বইটিতে লেখক প্রাচীন বাংলার দোহাকোষ ও চর্যাপদের কবিদের—যারা সমাজে নিম্নস্তরভুক্ত ছিলেন—তাদের বক্তব্য, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহকে বিশ্লেষণ করেছেন। সরহপাদ থেকে কঙ্কনপাদ—তারা ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৈষম্য, জাতিগত আধিপত্য ও ভণ্ড ধর্মীয় আচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। তাদের কণ্ঠই প্রাকৃতজনের যুক্তিবাদী প্রতিবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। কার্ল মার্কস দর্শনকে কেবল বিশ্বের বিশ্লেষণ নয় বরং পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছিলেন। এই আলোকে যতীন সরকারের লেখায় দেখা যায়—প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন কেবল অভিজ্ঞতা নয়; এটি পরিবর্তনের রাজনৈতিক সম্ভাবনার একটি উৎস, এবং সমাজের বৃহত্তর বাস্তবতা বোঝার বিকল্প দৃষ্টিকোণ।
যতীন সরকারের ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, কিন্তু চিন্তার স্তর গভীর। ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান—সব মিলিয়ে তিনি যে পাঠ নির্মাণ করেছেন তা গবেষণামূলক ও সাহিত্যময়তার এক ব্যতিক্রম সমন্বয়। বইটি পড়তে পড়তে পাঠক খুঁজে পাবেন বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, সংগ্রাম এবং মানবিক মূল্যবোধের বাস্তব আত্মস্বরূপ। মন হয়ে উঠবে অনুসন্ধানী। প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জীবনের সত্য কোনো অলৌকিক শক্তিতে নয়, বরং মানুষের শ্রম, ভালোবাসা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহমর্মিতায় নিহিত। বাংলার লোকদর্শন ও সাধারণ মানুষের চেতনার এই বইটি এক গুরুত্বপূর্ণ মানসিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ভ্রমণ। আর তাই লেখক নিজে আমাদের মনে করিয়ে দেন, -বইটি থাকবে।
লেখক-চন্দন কুমার লাহিড়ী, ঢাকা ।