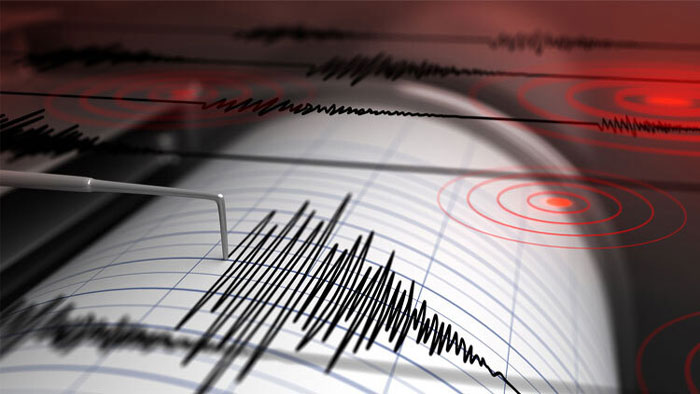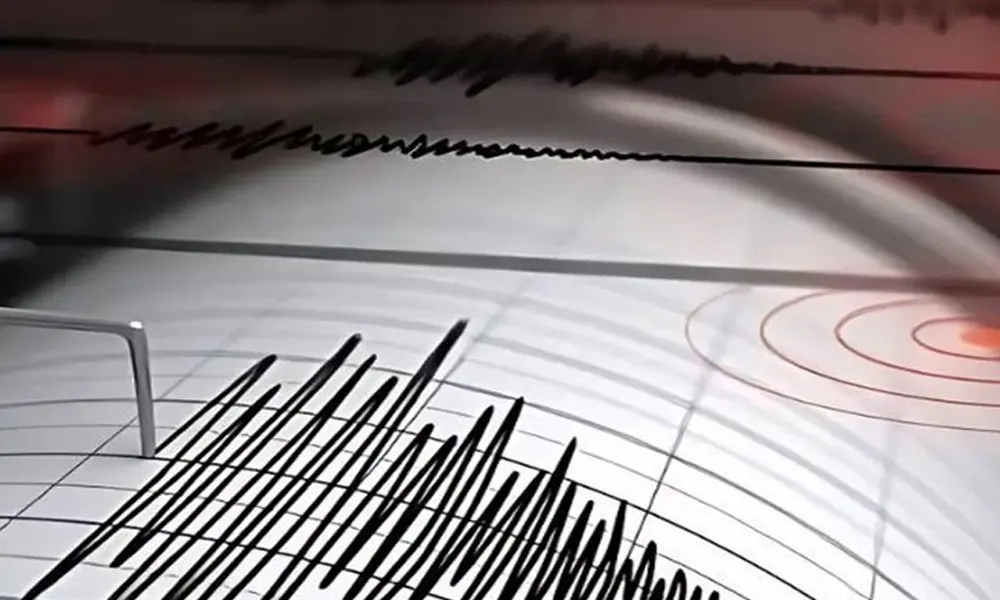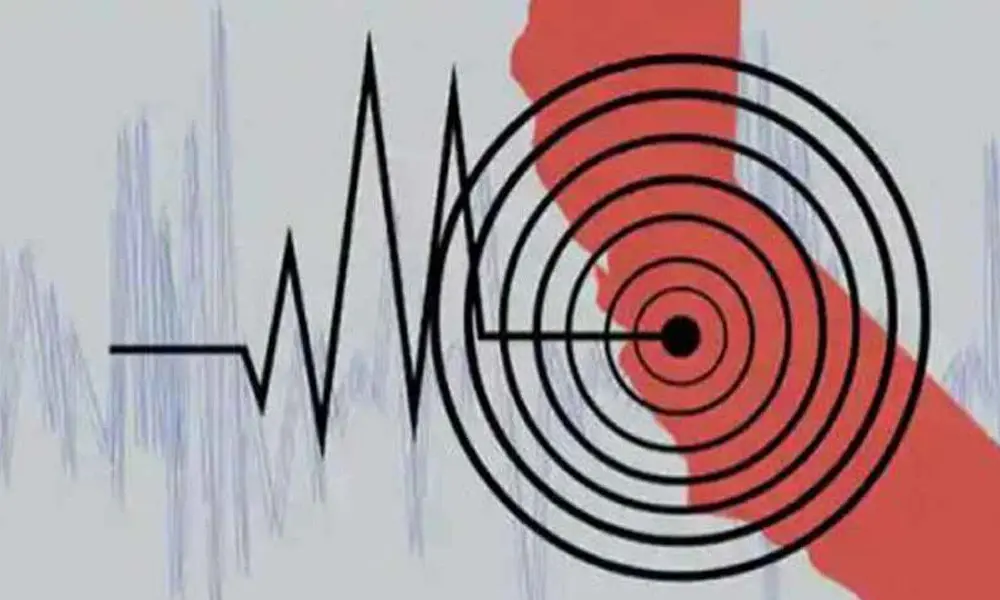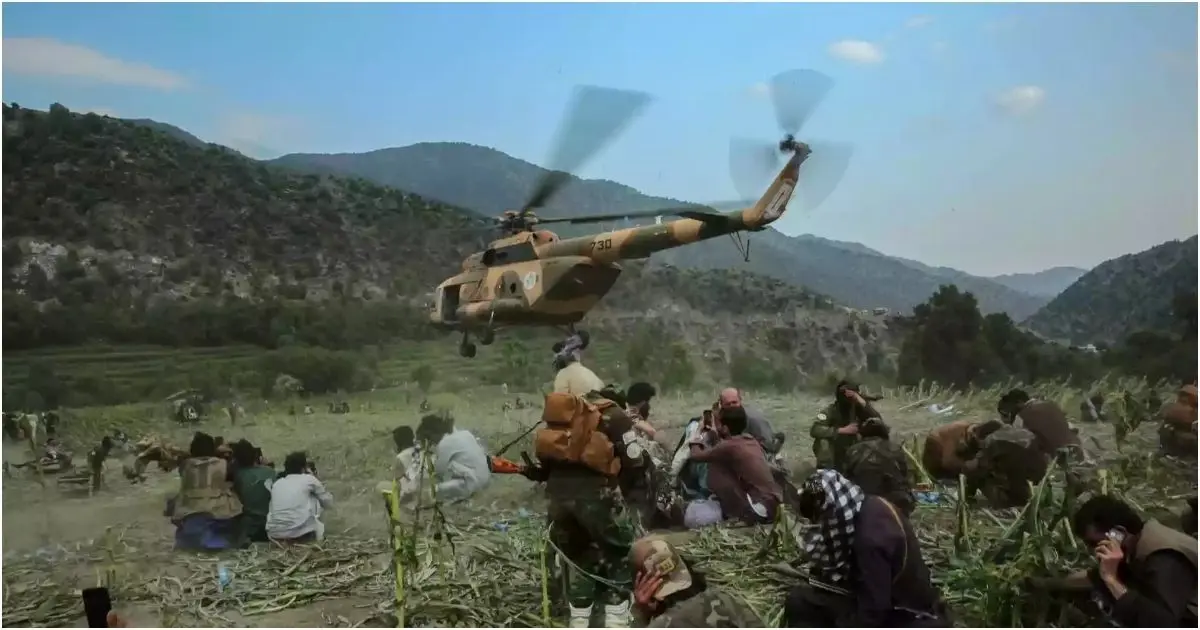কোনো কিছু কখন কাঁপে? সোজা কথায় উত্তর হলো, যখন বস্তুটাকে আঘাত করা হয়?
ভূমিকম্পের সময় পৃথিবীটাই যে কেঁপে ওঠে, একে তাহলে কে আঘাত করে?
পৃথিবীকে আঘাত করে ভূপৃষ্ঠের নিচে জমা হওয়া শক্তি। এই শক্তিগুলো আসলে কী? ধরা যাক, বহুদিন একটা জায়গায় গ্যাস জমা হয়েছে, এই গ্যাসের চাপ একসময় এত বেশি হয় যে পৃথিবীর ওপরের স্তরের শিলাগুলোকে ধাক্কা দেয়। সেই ধাক্কায় কেঁপে ওঠে পৃথিবী।
এই ধাক্কা দেওয়ার যে ব্যাপারটা ঘটছে, এটা শুধু গ্যাসীয় বস্তুর ক্ষেত্রে হচ্ছে, তা নয়।
হতে পারে ভূপৃষ্ঠের নিচে কোথাও গলিত লাভা জমা হয়েছে, সেখানকার তাপমাত্রা গেছে অনেক বেড়ে, তখন সেখানকার পদার্থগুলোর ঘনত্ব কমতে থাকবে, অণুগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে চাইবে। দূরে সরে যাওয়ার জন্য বাড়তি জায়গা তো দরকার। পদার্থগুলো যে জায়গায় আটকে ছিল, সে জায়গা তো বড় হচ্ছে না। তাই অণুগুলোর একটা বাড়তি চাপ তৈরি করবে।
যে জায়গায় ওইসব গলিত লাভা আটকে ছিল সে জায়গাটার দেয়ালগুলো অনুভব করবে বাড়তি চাপ। যখন চাপ খুব বেশি হবে, তখন ভূপৃষ্ঠ কেঁপে উঠবে।
আরও পড়ুন: প্রজাপতির ডানা ঝাপটানিতেই হতে পারে মহাপ্রলয় —কিভাবে, জানেন?
সব সময় লাভাগুলো বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু কখনো চাপ এত বেশি হয়, প্রচণ্ড শক্তিতে ভূপৃষ্ঠকে ধাক্কা দেয়।
আগেই বলেছি এই ধাক্কার কারণে ভূপৃষ্ঠে কম্পন ওঠে। কিন্তু যদি ভূপৃষ্ঠের কোথাও ফাটল থাকে বা দুর্বল কোনো জায়গা থাকে, সেখান থেকে প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে আসে লাভা। যেটাকে আমরা অগ্ন্যুৎপাত বলি। যে ফাটল থেকে লাভা বেরিয়ে আসে, সেটাকে বলা হয় অগ্নেয়গিরি। লাভা বেরিয়ে আসার সময় ভূপৃষ্ঠকে প্রবলভাবে ধাক্কা মারে।
ফলে কেঁপে কেঁপে ওঠে পৃথিবী।
কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশে কোনো কোনো অগ্নেয়গিরি নেই। তাহলে ভূমিকম্প কেন হচ্ছে বারবার?
আরও পড়ুন: ডিপফেক: সমালোচিত প্রযুক্তির আদ্যোপান্ত
আসলে লাভা উদগিরণ বা আগ্নেয়গিরিই ভূমিকম্পের একমাত্র কারণ নয়। গোটা পৃথিবীর ভূত্বক কয়েকটি ছোট-বড় প্লেটে বিভক্ত। এর মধ্যে রয়েছে সাতটা মহাদেশীয় প্লেট এবং বেশ কয়েকটি তুলনামূলক ছোট প্লেট। ভারতীয় উপমহাদেশীয় প্লেট এদের মধ্যে অন্যতম।
এসব প্লেট কিন্তু একেবারে স্থির নয়। খুব ধীরে হলেও এগুলো চলতে থাকে। চলতে চলতে কখনো একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কাও লাগে। যেমন ভারতীয় উপমহাদেশীয় প্লেট একসময় আফ্রিকার কাছাকাছি ছিল। ধীরে ধীরে এটা এশিয়ার দিকে সরে আসে, একসময় এশীয় প্লেটের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এর সঙ্গে যুক্ত হয়।
আরও পড়ুন : ঈশ্বরকে নোবেল পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন এক বিজ্ঞানী—কে তিনি
প্লেটগুলো কাছাকাছি এসে একে-অন্যের কিছুটা ওপরেও চলে আসতে পারে। তাই বলে সারা জীবন একটা প্লেট আরেকটা প্লেটের ওপরে চড়ে বসে থাকবে তা তো হবে না। প্রাকৃতিক কারণেই তাকে সরে আসতে হবে। আর এই সরে আসার চেষ্টা যখন চলে, তখনই ভূমিকম্প হয়।
আমাদের দেশে যেসব ভূমিকম্প হচ্ছে এর কারণ টেকটনিক প্লেট। উপমহাদেশীয় প্লেটের সঙ্গে এশীয় প্লেটের সংস্পর্শ আর সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলেই এত ভূমিকম্প এখন দেখা যাচ্ছে এ অঞ্চলে।
এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত লেখা আসছে শিগগির। চোখ রাখুন কালের কণ্ঠের বিজ্ঞান পেজে।
সূত্র : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক